“দেশের মূলধারার গণমাধ্যমগুলোর মধ্যে ভুয়া (ফেইক) সংবাদ প্রকাশ এবং পরবর্তীতে তা প্রত্যাহারের ঘটনা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।”
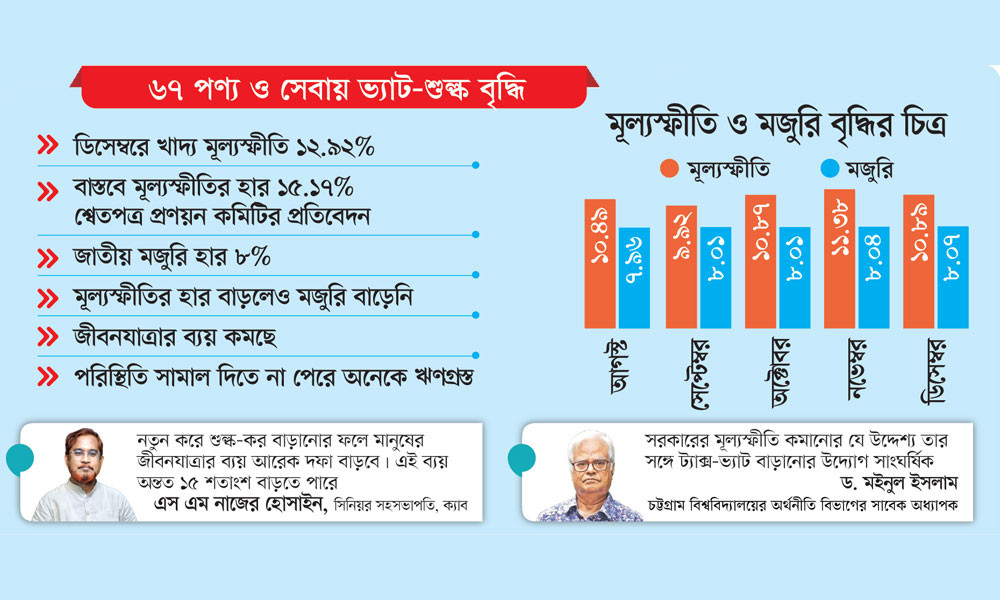
দেশের মূলধারার গণমাধ্যমগুলোতে ভুয়া (ফেইক) সংবাদ প্রকাশ ও পরবর্তীতে তা প্রত্যাহারের ঘটনা উদ্বেগজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সম্প্রতি প্রেস ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ (পিআইবি) আয়োজিত এক সেমিনারে প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদনে উঠে এসেছে, এই প্রবণতায় শীর্ষস্থানে রয়েছে দৈনিক প্রথম আলো। এর পরে রয়েছে দৈনিক কালবেলা এবং তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে দৈনিক ইত্তেফাক।
শনিবার (২৮ জুন) সকালে আয়োজিত ওই সেমিনারে গবেষণা প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন মামুন অর রশীদ, যিনি বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের ‘তথ্যপ্রযুক্তিতে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধকরণ (ইবিএলআইসিটি)’ প্রকল্পে পরামর্শক হিসেবে কর্মরত। তাঁর গবেষণার শিরোনাম ছিল—‘বাংলাদেশের গণমাধ্যমের সাম্প্রতিক অপতথ্যের গতি-প্রকৃতি’।
গবেষণায় দেখা গেছে, ২০২৩ সালের ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার আন্দোলনের পর থেকে মূলধারার সংবাদমাধ্যমগুলোতে ভুয়া সংবাদের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়, অনেক ক্ষেত্রে বস্তুনিষ্ঠতা ও সাংবাদিকতার নীতির চেয়ে ভাইরাল হওয়ার প্রতিযোগিতাই হয়ে উঠেছে প্রকাশনার মূল লক্ষ্য।
২০২৪ সালের জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত সময়কালে দেশের মূলধারার গণমাধ্যমগুলোতে ভুয়া সংবাদ প্রকাশ ও তা পরবর্তীতে প্রত্যাহারের ঘটনা উদ্বেগজনক হারে বেড়েছে। প্রেস ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ (পিআইবি) আয়োজিত এক সেমিনারে মামুন অর রশীদের উপস্থাপিত গবেষণা অনুযায়ী, সবচেয়ে বেশি সংবাদ প্রত্যাহার করতে হয়েছে দৈনিক প্রথম আলোকে। তালিকায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে যথাক্রমে দৈনিক কালবেলা ও দৈনিক ইত্তেফাক।
গবেষণায় আরও জানানো হয়, অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গণমাধ্যমগুলোর মধ্যে রয়েছে—দৈনিক যুগান্তর, ডেইলি স্টার, ঢাকা পোস্ট, বাংলা ট্রিবিউন, বিডিনিউজ, কালের কণ্ঠ, যমুনা টিভি, বিবিসি বাংলা, চ্যানেল২৪বিডি, সময় নিউজ, জাগো নিউজ২৪, বাংলানিউজ২৪, জনকণ্ঠ, ঢাকা ট্রিবিউন, টিবিএস, দেশ রূপান্তর, ইনকিলাব, আইটিভি (ইন্ডিপেন্ডেন্ট টিভি), সময়ের কণ্ঠস্বর, একাত্তর টিভি, এনটিভি ওয়েব, যায়যায়দিন, আমাদের সময়, সময়ের আলো এবং বিডি প্রতিদিন।
মামুন অর রশীদ বলেন, “এটি আমার নিজস্ব গবেষণা কর্ম, যা ২০২৪ সালের জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত সময়কালজুড়ে পরিচালিত হয়েছে। গবেষণাটি একটি জার্নালে প্রকাশের জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে এবং আরও তথ্য হালনাগাদ চলছে।”
উক্ত গবেষণায় ছয় মাসের ফ্যাক্ট-চেক সাইট থেকে সংগৃহীত স্ক্র্যাপ ডেটা, মূলধারার সংবাদমাধ্যমের ৬৯৪টি ‘ডেড লিংক’, এবং পাঁচটি বিশ্লেষণ পদ্ধতির ব্যবহার উল্লেখ করা হয়েছে।
সেমিনারের প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রীর ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তিবিষয়ক বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব শঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, “আগামী জাতীয় নির্বাচনকে ঘিরে ভুয়া ও মিথ্যা তথ্যের বিস্তার বাড়তে পারে। রাজনৈতিক দল বা প্রার্থীরা একে অপরের বিরুদ্ধে অপতথ্য ছড়াতে পারে।”
তিনি আরও বলেন, “বানোয়াট ও চাঞ্চল্যকর তথ্য মানুষ বেশি বিশ্বাস করে, পছন্দও করে। ২০২৩ সালের ৫ আগস্টের ঘটনার পর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আওয়ামী লীগের উপস্থিতিও দৃশ্যমানভাবে বেড়েছে।”
বর্তমানে সংবাদ প্রকাশের ক্ষেত্রে অনেক গণমাধ্যমে সত্যের চেয়ে ভাইরাল হওয়ার দিকেই গুরুত্ব বেশি দেওয়া হচ্ছে, যা গণমাধ্যমের নৈতিকতা ও দায়িত্ববোধ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। প্রেস ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ (পিআইবি) আয়োজিত এক সেমিনারে এসব মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রীর তথ্যপ্রযুক্তি উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব।
তিনি বলেন, “ভাইরাল সংবাদের একটি বাণিজ্যিক ও আর্থিক মূল্য রয়েছে, তাই অনেক গণমাধ্যম উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এমন সংবাদ প্রকাশ করছে। এই প্রবণতা অব্যাহত থাকলে গণমাধ্যমগুলো ক্রমেই বিশ্বাসযোগ্যতা হারাবে, এবং সে শূন্যস্থান দখল করবে কনটেন্ট মেকার বা ব্লগাররা।”
গণমাধ্যমের সংকট মোকাবিলায় ডিজিটাল ভেরিফিকেশন, ফ্যাক্ট চেকিং ও প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ বাড়ানোর ওপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি।
সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের ‘ইবিএলআইসিটি’ প্রকল্পের পরামর্শক মামুন অর রশীদ। তিনি তার গবেষণাপত্রে তুলে ধরেন, গত ৬ মাসে দেশে ভুয়া সংবাদের মাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে এবং সংবাদমাধ্যমগুলোকে এর দায় নিতে হবে।
সেমিনারের সভাপতিত্ব করেন পিআইবির মহাপরিচালক ফারুক ওয়াসিফ। সূচনা বক্তব্যে তিনি বলেন, “বিগত ১৫ বছরে রাষ্ট্র নিজেই মিথ্যার কারখানায় পরিণত হয়েছিল, আর সংবাদমাধ্যম ছিল তার ফেরিওয়ালা।” তিনি অভিযোগ করেন, গ্রেপ্তার, নির্যাতন, গুমের পক্ষে সাংবাদিকতা করা হয়েছে, এমনকি বিবিএস-এর মতো সংস্থাও মিথ্যা তথ্য ছড়িয়েছে।
ফারুক ওয়াসিফ আরও বলেন, “শুধু ফ্যাক্ট-চেক দিয়ে অপতথ্য মোকাবিলা সম্ভব নয়, এটি একটি সামাজিক আন্দোলনে রূপ দিতে হবে। দায়বদ্ধ সাংবাদিকতা ফিরিয়ে আনার জন্য এটাই সময়।”
সেমিনারে আলোচনায় অংশ নেন আমার দেশ পত্রিকার চিফ রিপোর্টার বাছির জামাল, প্রথমা প্রকাশনার প্রধান সমন্বয়কারী মশিউল আলম, একাত্তর টিভির সিওও শফিক আহমেদ, যুগান্তরের নগর সম্পাদক মিজান মালিক, এবং যমুনা টিভির মাহফুজ মিশু প্রমুখ। আলোচনায় গণমাধ্যমকর্মীদের দক্ষতা উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তিগত বিনিয়োগের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি বিশেষভাবে উঠে আসে।
সেমিনারটি সঞ্চালনা করেন পিআইবির জ্যেষ্ঠ গবেষণা কর্মকর্তা গোলাম মোর্শেদ।

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন
গবেষণাটি কে পরিচালনা করেছে এবং কোথায় উপস্থাপন করা হয়েছে?
গবেষণাটি পরিচালনা করেছেন মামুন অর রশীদ, যিনি বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের ইবিএলআইসিটি প্রকল্পের পরামর্শক। এটি উপস্থাপন করা হয়েছে প্রেস ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ (পিআইবি) আয়োজিত এক সেমিনারে।
গবেষণায় কোন সময়সীমার সংবাদ বিশ্লেষণ করা হয়েছে?
গবেষণাটি ২০২৪ সালের জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত সময়কালকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হয়েছে। এই ছয় মাসের মধ্যে সংবাদমাধ্যমগুলোর ভুল বা ভুয়া সংবাদ প্রকাশ ও তা পরবর্তীতে প্রত্যাহারের তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়।
কোন সংবাদমাধ্যমগুলো ভুল সংবাদ প্রত্যাহারে শীর্ষে রয়েছে?
প্রথম অবস্থানে রয়েছে দৈনিক প্রথম আলো, দ্বিতীয় দৈনিক কালবেলা, এবং তৃতীয় দৈনিক ইত্তেফাক। এছাড়া তালিকায় আছে যুগান্তর, ডেইলি স্টার, ঢাকা পোস্ট, বাংলা ট্রিবিউন, বিডিনিউজ২৪, কালের কণ্ঠ, যমুনা টিভি, বিবিসি বাংলা, সময় নিউজসহ আরও অনেকে।
গণমাধ্যমে ভুল সংবাদের এই প্রবণতা কেন বাড়ছে বলে গবেষণায় বলা হয়েছে?
গবেষণায় দেখা গেছে, অনেক সংবাদ ভাইরাল হওয়ার উদ্দেশ্যে বস্তুনিষ্ঠতা না মেনে প্রকাশ করা হচ্ছে। এমনকি এই ধরনের ভাইরাল সংবাদের পেছনে বাণিজ্যিক ও আর্থিক স্বার্থ কাজ করছে বলেও মন্তব্য করা হয়েছে।
এই সংকট মোকাবেলায় কী পরামর্শ দেওয়া হয়েছে?
প্রধান অতিথি ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব এবং গবেষক মামুন অর রশীদ উভয়েই গণমাধ্যম মালিক ও ব্যবস্থাপনাকে ডিজিটাল ভেরিফিকেশন, ফ্যাক্ট-চেকিং প্রযুক্তি ও সাংবাদিকদের দক্ষতা উন্নয়ন-এ বিনিয়োগের পরামর্শ দিয়েছেন। একইসঙ্গে অপতথ্য রোধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তাও তুলে ধরা হয়েছে।
উপসংহার
সাম্প্রতিক গবেষণায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে দেশের মূলধারার গণমাধ্যমগুলোতে ভুল ও ভুয়া সংবাদ প্রকাশ এবং পরে তা প্রত্যাহারের প্রবণতা আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে। এতে শুধু গণমাধ্যমের পেশাগত নৈতিকতা ও দায়িত্ববোধ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে না, বরং সার্বিকভাবে গণতন্ত্র, সামাজিক স্থিতিশীলতা এবং জনগণের তথ্য জানার অধিকারও হুমকির মুখে পড়ছে।
গণমাধ্যমের বিশ্বাসযোগ্যতা যখন প্রশ্নবিদ্ধ হয়, তখন বিকল্প তথ্য উৎস হিসেবে অনিয়ন্ত্রিত কনটেন্ট মেকার ও ব্লগারদের উত্থান ঘটে, যা আরও ভুয়া ও বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়ানোর ঝুঁকি তৈরি করে।







