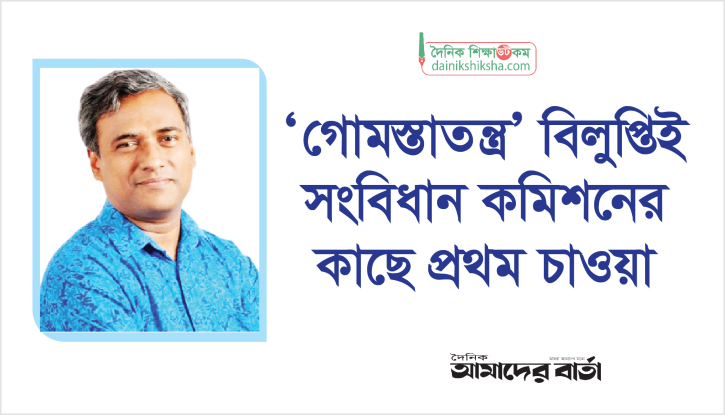সংবিধানে রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে উল্লেখ করে, অন্যতম সংবিধান প্রণেতা ও বিশিষ্ট আইনজীবী ড. কামাল হোসেন বলেছিলেন, “দেখুন, ওটা দিয়ে মাপতে গেলে এগুলো তো কোনো রাজনৈতিক দল নয়। রাজনৈতিক পারিবারিক ভিত্তিতে একটা জমিদারি স্থাপন করা হয়েছে। লিডার তো নয়, এরা অনেকেই গোমস্তা।”
একটি দেড় যুগ পুরনো আলাপচারিতায়, ড. কামাল হোসেন আরও বলেছিলেন, “আমার দাদার আমলে আমি বরিশালে জমিদারি দেখেছি। সেখানে মুনশিজি থাকতেন। খাতা লিখতেন। গোমস্তারা প্রজাদের কাছ থেকে তুলতেন। এখনো সেই ধারাই দেখছি।”
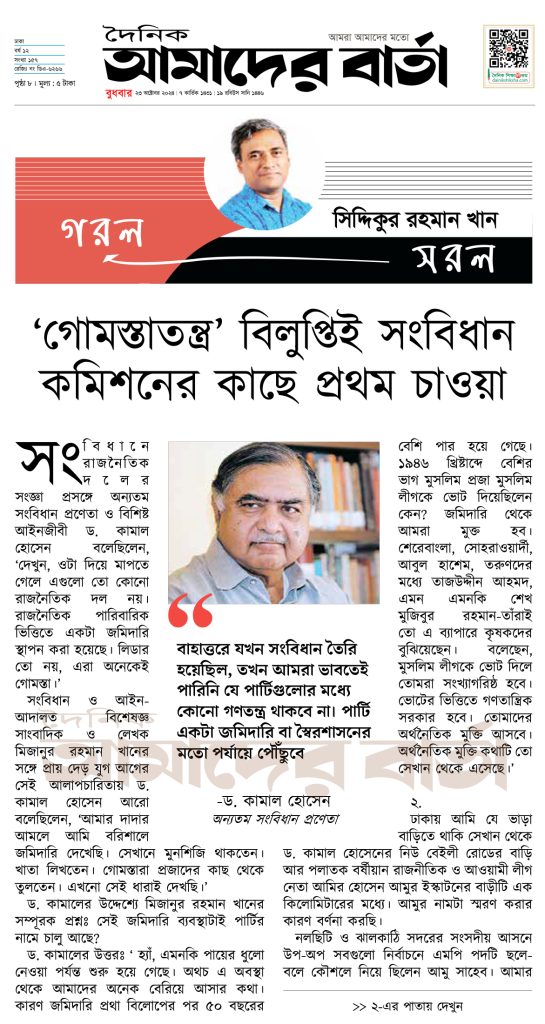
“ঢাকায় আমি যে ভাড়া বাড়িতে থাকি, সেখান থেকে ড. কামাল হোসেনের নিউ বেইলী রোডের বাড়ি এবং পলাতক বর্ষীয়ান রাজনীতিক, টাকার জাজিমে ঘুমানো আওয়ামী লীগ নেতা আমির হোসেন আমুর ইস্কাটনের বাড়িটি এক কিলোমিটারের মধ্যে অবস্থিত। আমুর নামটা স্মরণ করার কারণ বর্ণনা করছি।”
এখানে, লেখক তাঁর আশেপাশের রাজনৈতিক পরিবেশ এবং পরিচিত ব্যক্তিদের উল্লেখ করছেন। আমির হোসেন আমুর নামের উল্লেখের মাধ্যমে লেখক কিছু নির্দিষ্ট রাজনৈতিক পরিস্থিতি বা চরিত্রের প্রতি ইঙ্গিত দিচ্ছেন, যা পরবর্তী বর্ণনায় বিশদভাবে পরিষ্কার হতে পারে।
“নলছিটি ও ঝালকাঠি সদরের সংসদীয় আসনে দুই-তিনটি বাদে প্রায় সবগুলো নির্বাচনে এমপি পদটি ছলে-বলে কৌশলে নিয়েছিলেন আমু সাহেব। আমার জন্মস্থানও নলছিটি, এবং ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি, আমু সাহেবকে পায়ে হাত দিয়ে সালাম করেন নেতা-কর্মীরা। ভক্তিসহ সালাম করা দোষের কিছু নয়, তবে আমু সাহেবের সালাম নেওয়া ছিল বাধ্যতামূলক। এই পরিস্থিতি ছিল ঠিক তেমনি, যেটা ড. কামাল হোসেন বর্ণিত ‘পায়ের ধুলা নেওয়া শুরু হয়ে গেছে’—অর্থাৎ একটি প্রথা যা সম্মানের চেয়ে শক্তি ও কর্তৃত্বের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমু সাহেব এবং তাঁর মতো নেতারা এই ‘ধুলা নেওয়ার’ সংস্কৃতির পথ প্রদর্শক হতে পারেন। পরবর্তীতে তা সংক্রামক হয়ে, রাজনৈতিক পরিবেশে পচন ধরে, ৫ আগস্টে গিয়ে কিছুটা সাময়িক বিরতি নিয়েছে। তবে এই বিরতির মধ্যে সংবিধান সংস্কার কমিশন কি নতুন উদ্যোগ নিতে পারে? এমন চিন্তা থেকেই এই লেখা। বর্তমান সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রধান ড. আলী রিয়াজ প্রায়শই প্রয়াত মিজানুর রহমান খানকে স্মরণ করেন। গত বছরের ১১ জানুয়ারি তিনি তাঁর ফেসবুকে লেখেন, ‘…তার লেখা বই হাতে নিয়ে পাঠ করি, নাড়াচাড়া করি। সংবিধানের বিভিন্ন অনুচ্ছেদের আলোচনা পড়ি, ভাবি মিজান এই বিষয়ে কী বলতেন।'”
মিজানুর রহমান খান সেদিন ড. কামাল হোসেনের কাছে প্রশ্ন করেছিলেন, “দ্বিকক্ষবিশিষ্ট পার্লামেন্ট নিয়ে কি ভাবার সময় এসেছে?” ড. কামাল হোসেনের উত্তর ছিল এমন:
“এক অর্থে অবশ্যই এসেছে। তবে অধ্যাপক বদরুদ্দোজা চৌধুরী [প্রয়াত রাষ্ট্রপতি] সাহেবদের একটা প্রস্তাব আমরা সমর্থন করেছি। সেটা হলো ৪০০ আসনের একটা পার্লামেন্ট প্রতিষ্ঠা করা। ৩০০ আসনে প্রত্যক্ষ নির্বাচন হবে, আর বাকি ১০০ আসনে হবে পরোক্ষ নির্বাচন। এটা এক ধরনের অনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব। সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী দলগুলো এই নতুন ১০০ আসনের জন্য অভিজ্ঞ, বিশেষজ্ঞ—অর্থাৎ অন্য দেশে যারা আপার হাউস বা উচ্চ কক্ষে যান, তেমন লোকের নাম প্রস্তাব করবে।”
এই পর্যায়ে মিজানুর রহমান খান মনে করিয়ে দেন, “ব্রিটেনে যেমনটা আছে?” উত্তরে ড. কামাল হোসেন বলেন, “ভারতের রাজ্যসভাতেও আছে। বিভিন্ন মহলের, যেমন বিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ, কূটনীতিবিদ—সংসদের ৩০০ আসনে নির্বাচিত সদস্যরা পরোক্ষভাবে তাঁদের নির্বাচন করবেন। আমরা বলছি, ওভাবে পরোক্ষভাবে নির্বাচিত না করে তাঁদের আনুপাতিক হারে মনোনীত হতে দিন। প্রত্যেক দলের কাছে একটি তালিকা থাকবে। যেমন বিএনপি ও আওয়ামী লীগের তালিকায় তাদের পছন্দের বুদ্ধিজীবী, শিক্ষাবিদ বা বিশেষজ্ঞদের নাম থাকবে।”
এ পর্যায়ে মিজানুর রহমান খান প্রশ্ন করেন, “অনুপাত বণ্টনের ভিত্তি কী হবে?” উত্তরে ড. কামাল হোসেন বলেন, “কোনো দল যদি ৩০ শতাংশ ভোট পায়, তাহলে তারা ওই ১০০ আসন থেকে ৩০ ভাগ সদস্য নির্বাচন করতে পারবে।”
এরপর মিজানুর রহমান খান জানতে চান, “এই ১০০ আসনে কোনো ভোটাভুটি হবে না?” ড. কামাল হোসেনের উত্তর ছিল, “না। ব্যক্তিগতভাবে ভোটাভুটি হবে না। এই ১০০ আসনের নির্বাচনে কোনো প্রচারণা থাকবে না। কোটি টাকাও খরচ করতে হবে না। বর্তমান আসনব্যবস্থাকে ৩০০ আসনে ভাগ করা যায়, আবার না করলেও চলে।”
মিজানুর রহমান খানের প্রশ্ন ছিলো, “১০০ আসন কি কোনো নির্বাচনী এলাকার ভিত্তিতে হবে না? ভোটাভুটি ছাড়াও তো পুরো দেশকে ১০০ আসনে ভাগ করা যায়।”
ড. কামাল হোসেনের মন্তব্য ছিল, “ঠিকই বলেছেন। শ্রীলঙ্কা কিন্তু করেছে আসনওয়ারি। তাতে লাভও হয়। সংশ্লিষ্ট আসনের লোকদের সঙ্গে মনোনীত সংসদ সদস্যদের একটা যোগাযোগও থাকে। আর তিনি তাঁর এলাকার মানুষের মতামতকে একদম উপেক্ষাও করতে পারেন না। ভাবতে খুব কষ্ট হয়, বাংলাদেশে পার্টি ও পার্টি লিডারশিপ তো জমিদারি ব্যবস্থায় পরিণত হয়ে গেছে। আমাদের তো ন্যূনতম ‘পার্টি কনসেপ্ট’ বা দলীয় ধারণা অনুপস্থিত।”
মিজানুর রহমান খানের প্রশ্ন ছিলো: “১০০ আসন কি কোনো নির্বাচনী এলাকার ভিত্তিতে হবে না? ভোটাভুটি ছাড়াও তো পুরো দেশকে ১০০ আসনে ভাগ করা যায়।”
ড. কামাল হোসেনের মন্তব্য ছিল, “ঠিকই বলেছেন। শ্রীলঙ্কা কিন্তু করেছে আসনওয়ারি। তাতে লাভও হয়। সংশ্লিষ্ট আসনের লোকদের সঙ্গে মনোনীত সংসদ সদস্যদের একটা যোগাযোগও থাকে। আর তিনি তাঁর এলাকার মানুষের মতামতকে একদম উপেক্ষাও করতে পারেন না। ভাবতে খুব কষ্ট হয়, বাংলাদেশে পার্টি ও পার্টি লিডারশিপ তো জমিদারি ব্যবস্থায় পরিণত হয়ে গেছে। আমাদের তো ন্যূনতম ‘পার্টি কনসেপ্ট’ বা দলীয় ধারণা অনুপস্থিত।”
ড. কামাল হোসেনের আরও মন্তব্য ছিল, “বাহাত্তরে যখন সংবিধান তৈরি হয়েছিল, তখন আমরা ভাবতেই পারিনি যে পার্টিগুলোর মধ্যে কোনো গণতন্ত্র থাকবে না। পার্টি একটা জমিদারি বা স্বৈরশাসনের মতো পর্যায়ে পৌঁছুবে।”
বাহাত্তরের সংবিধান লেখার সময় উচ্চ কক্ষের কথা কি আদৌ আলোচনায় এসেছিল? এমন প্রশ্নের জবাবে ড. কামাল বলেন, “এ সব কথাই আজ আমাদের বলতে হবে। কেননা আমাদের এতো বিশ্বাস ছিল যে, দ্বিকক্ষবিশিষ্ট পার্লামেন্ট লাগবে না।”
‘গোমস্তাতন্ত্র’ কী?
‘গোমস্তাতন্ত্র’ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে বাংলাদেশে রাজনৈতিক পরিবেশ ও দলের অভ্যন্তরীণ শাসন কাঠামো বোঝাতে। এটি এমন এক ব্যবস্থাকে নির্দেশ করে যেখানে রাজনৈতিক দলগুলো পারিবারিক বা জমিদারি ভিত্তিতে পরিচালিত হয়, এবং নেতাদের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন বাধ্যতামূলক হয়ে ওঠে।
কেন ‘গোমস্তাতন্ত্র’ বিলুপ্তির দাবি উঠেছে?
‘গোমস্তাতন্ত্র’ রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরীণ শাসনে স্বৈরাচারের মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি করে, যেখানে দলের নেতা বা কর্তৃপক্ষের প্রতি আনুগত্য না দেখালে, সদস্যরা স্বীকৃতির বাইরে চলে যান। এটি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পরিপন্থী এবং দলীয় স্বাধীনতার অভাব সৃষ্টি করে।
‘গোমস্তাতন্ত্র’ বিলুপ্তির জন্য কি পদক্ষেপ নেওয়া হবে?
সংবিধান কমিশনের কাছে প্রথম চাওয়া ‘গোমস্তাতন্ত্র’ বিলুপ্তি। এর মানে হলো রাজনৈতিক দলগুলোর পরিচালনা ও সদস্য নির্বাচন প্রক্রিয়া স্বচ্ছ, গণতান্ত্রিক এবং মুক্ত করার লক্ষ্যে আইনগত সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া।
কিভাবে ‘গোমস্তাতন্ত্র’ বিলুপ্তি সংবিধান সংস্কারের সঙ্গে সম্পর্কিত?
সংবিধান সংস্কার কমিশনের মাধ্যমে, রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরীণ শাসন ব্যবস্থা সংস্কার করে একটি গণতান্ত্রিক পরিবেশ নিশ্চিত করতে ‘গোমস্তাতন্ত্র’ বিলুপ্তির প্রস্তাব করা হয়েছে। এটি দলীয় নির্বাচনে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি প্রয়োগ এবং অনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে রাজনৈতিক নেতৃত্ব নির্বাচনকে সহজতর করবে।
কীভাবে এই বিলুপ্তি দেশের রাজনীতিতে পরিবর্তন আনবে?
‘গোমস্তাতন্ত্র’ বিলুপ্তি হলে, রাজনৈতিক দলের ভিতরে নেতৃত্ব নির্বাচনে স্বচ্ছতা এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হবে, যা দলগুলোর মধ্যে শক্তি ভারসাম্য সৃষ্টি করবে। এতে দলীয় শৃঙ্খলা এবং সরকারের কার্যক্ষমতা বাড়বে।
উপসংহার
উপসংহারে বলা যায়, ‘গোমস্তাতন্ত্র’ বিলুপ্তির দাবি বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির উন্নয়নে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে। এই সংস্কারের মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে স্বচ্ছতা, গণতন্ত্র এবং সুষম প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত হবে। বর্তমান পরিস্থিতিতে, যেখানে নেতাদের প্রতি আনুগত্য এবং স্বৈরাচারী আচরণ প্রাধান্য পাচ্ছে, ‘গোমস্তাতন্ত্র’ বিলুপ্তি রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে শক্তিশালী গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি করবে। এর ফলে, দেশের শাসনব্যবস্থা আরও কার্যকর, সুশাসিত এবং জনগণের প্রতি দায়বদ্ধ হবে। সংবিধান সংস্কার কমিশন এই পদক্ষেপের মাধ্যমে বাংলাদেশে গণতন্ত্রের বাস্তবায়নকে আরও সুসংহত করতে চায়, যা দেশের ভবিষ্যত রাজনীতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।